সৌম্য ঘোষ
জসীমউদ্দীনের আবহমান গ্ৰামীন
"""""""""""""""""""'''''''""""
সংস্কৃতির কবিতা
""""""""""""""""""""""""""""""
ত্রিশ দশকের কবিদের দাপট ভেঙে সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বকীয়তা বঙ্গজ উপাদান নিয়ে কবিতা নির্মাণে দক্ষতা দেখিয়েছেন কবি জসীমউদ্দীন। কবিতার সমস্ত উপাদান—চিত্রকল্প, অলংকার, ছন্দ, রস প্রভৃতি----
বাঙালির। দেশজ। এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির।
জসীমউদ্দীন বাংলার গ্রামীণ জীবনের ভাষ্যকার। গ্রাম্যসমাজ ও গ্রাম্যজীবন তাঁর কবিতার ক্যানভাসে চিত্রিত হয়েছে ভাষ্যকারের বিবৃতিতে। গ্রামজীবনের প্রতিচিত্র নির্মাণের পাশাপাশি তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মানববোধকে লালন ও সমৃদ্ধ করেছেন। স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল কবিতা-নির্মাতা জসীমউদ্দীনের কাব্য-পরিসরের মূল্যায়ন আজো যথার্থভাবে হয়ে ওঠেনি। মানবপ্রীতি ও জীবন-সঙ্কটের সাথে একাত্ম যে জসীমউদ্দীন, তাঁকে আমরা আবিষ্কার করতে পারছি না নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণের অভাবে।
তাঁর ভাবনার-ব্যাপকতা সমকাল পেরিয়ে উত্তরকাল এবং আপন-বিবর ছাড়িয়ে বিশ্ব-পরিসরে প্রসারিত। ‘পল্লীকবি’ বা ‘গ্রামীণ কবি’ প্রভৃতি খণ্ডিত বিবেচনার মধ্যেও তেমন কোনো মাহাত্ম্য নেই। কেননা, তাঁর চিন্তাভুবনে কেবল গ্রাম নয়, আধুনিক শিল্প-ভাবনার বিচিত্র বিষয় জায়গা করে নিয়েছে কালের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুখপাত্র। গ্রামের কবি হিসাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে ‘দগ্ধগ্রামের’ ভাষ্যকার জসীমকে আমরা চিনতে ভুল করি। আর তাঁর প্রতিবাদী প্রবল কণ্ঠস্বরটি তাই আমাদের দৃষ্টি-সীমানার বাইরেই পড়ে থাকে পরম অবহেলায়। এই প্রতিবাদী চেতনাটি তিনি লাভ করেছেন সমকালের সামাজিক অশিক্ষা-অজ্ঞতা-অনাচার-অবহেলা আর মানুষের জীবন-বাস্তবতার ভেতরে লুকিয়ে থাকা না-বলা সব যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অনুভব থেকে। তাঁর কবিতায় বাঙালি জাতিসত্তার যে বীজ রোপিত, তা বাংলা কাব্যসভায় অনন্যসাধারণ। জসীমউদ্দীন বাংলা ভাষার একমাত্র কবি, যিনি ছিলেন একাধারে লোকায়তিক, আধুনিক, গ্রামীণ, স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক।
জসীমউদ্দীনের আখ্যানমূলক কাব্যের চারটি হচ্ছে : ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ (১৯২৯), ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ (১৯৩৩), ‘সকিনা’ (১৯৫৯) ও ‘মা যে জননী কান্দে’ (১৯৬৩)। আখ্যানমূলক কাব্যগুলির শব্দাবলি বা উপাদানগুলি পরিচিত পরিবেশের। সবুজবাংলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাদান। কিন্তু মাইকেল, নজরুল বা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি আখ্যান বা কবিতায় রামায়ণ-মহাভারত, লোকপুরাণ বা ধর্মীয় ঐতিহ্যের কাছে হাত পেতেছেন। এক্ষেত্রে জসীমউদ্দীন ব্যতিক্রম এবং অনন্য। তাঁর আখ্যানকাব্যে জনপ্রিয়তা ও নির্মাণশৈলীতে অনন্য। জসীমউদ্দীনের অন্ত্যমিলের কবিতাগুলো কানে সমধুর ঝংকার তোলে। ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য। ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ও জনপ্রিয় কাব্য। এ দুটি আখ্যানকাব্যে হিন্দু-মুসলিমদের সহাবস্থান, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও তৎকালীন পরিবেশ ও ঘটনা পরিক্রমায় লিখিত। রাখালী(১৯২৭) কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া ‘বালুচর’ (১৯৩০), ‘ধানখেত’(১৯৩৩), ‘হাসু’(১৯৩৮), ‘মাটির কান্না’(১৯৫১), ‘এক পয়সার বাঁশি’(১৯৫৬), ‘হলুদ বরণী’ (১৯৬৬), ‘জলে লেখন’(১৯৬৯), ‘পদ্মা নদীর দেশে’(১৯৬৯), ‘দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি’(১৯৮৭) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। জসীমউদ্দীনের ‘হাসু’ চমৎকার একটি শিশুতোষ কাব্য। শিশুমনকে নাড়া দেওয়ার মতো অনেক ছড়া আছে এ গ্রন্থে। ‘আমার বাড়ী’ ছড়াংশ—
''আমার বাড়ী যাইও ভ্রমর বসতে দেব পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেব শালিধানের চিড়ে।"
ছোটবেলা থেকেই সৌন্দর্যের প্রতি খুব প্রবল আগ্রহ ছিল। নদী, প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করতেন তিনি। ‘মুখখানা যেন সিন্দুরের মতো ডুগু ডুগু করে’ বলে উজ্জ্বল নারীর প্রতি টানের কথা বোঝা যায়। সে সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের বাস ছিল বৃহত্তর ফরিদপুর। বলা যায় বাংলার অনেকস্থানে। মাঝেমধ্যে সম্প্রীতির ফাটল দেখা যেত। এসব নিয়ে কবিতায় তুলে ধরেছেন তিনি। তবে হিন্দুদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল তাঁর ছোটবেলা থেকেই। হিন্দু রমণীদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন তিনি। কবির নিষ্পাপ চোখের বর্ণনা পাই আমরা বিভিন্ন কবিতায়, আখ্যানকাব্যে। ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ আখ্যানকাব্যে সাজুর সৌন্দর্য যেমন দেখি ‘লাল মোরগের পাখা’, তেমনই ‘তুলসীতলার প্রদীপ, তুলসীফুলের মঞ্জুরী কি দেব দেউলের ধূপ’, ‘সাঁঝ সকালের রঙিন মেঘেরা, ইত্যাদি সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ করা যায়। চিত্রকল্প নির্মাণ করতে যেয়ে বিভিন্ন অলংকার (উপমা ইত্যাদি) দেশের কাছেই হাত পেতেছেন তিনি। কিছু কিছু অংশ (তাঁর কবিতা থেকে) তুলে ধরলেই তা পরিষ্কার হবে। নারীর অনুভব খুব গভীরতর। নারী ও প্রকৃতি মিলে দারুণ প্রকাশে ব্যঞ্জনা পেয়েছে জসীমউদদীনের কবিতায়। বাঙালি সংস্কৃতি নিয়েই তাঁর কবিতায় ওজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছেঃ
'‘ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি/ শিশির ভেজা ঘাসে/ সারারাতের স্বপন আমার/ মিঠেল রোদে হাসে।’'
জসীমউদ্দীন বাংলার গ্রাম্য উপাদান নিয়ে প্রকৃতিকে আধুনিকতা দিয়েছেন। তাঁর কবিতা পাঠকের হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে। গ্রামীণ জনপদের সমস্ত অস্তিত্বে কবি জসীমউদদীন মিশে গেছেন; বৃহত্তর বাংলার কৃষকসমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় বোঝাপড়াটা ভালোই জমেছিল; তাঁর কবিতাতেই প্রমাণ। ‘‘রাখাল ছেলে’’ কবিতা থেকে :
‘'ঝাউয়ের ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ-পাগল বুড়ী,/আমরা সেথা চষতে লাঙল মুর্শীদা-গান জুড়ি।’'
কাশফুলের গুচ্ছ, বালুচর, সরিষা, শিশির, মিঠেল রোদ, রঙিন কাঁথা, বুনো ফুল, ফড়িং, টিয়া, ঘুঘু, ইত্যাদি—গ্রামের প্রতিবেশ, ছবি--অনায়াসেই এনেছেন কবিতার ছত্রে।
‘'ফোঁটা সরিষার পাপড়ির ভরে, চরো মাঠখানি কাঁপে/ থরে থরে সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে কাঁদিয়া ঝরে—/ বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে বালুর চরে (বালুচর)"
‘'মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল,/ তেল-হলুদে কানায় কানায় করছে ছলাৎ ছল(পরিচ্ছেদ ৪, নকশী কাঁথার মাঠ)’'
‘‘পল্লী বর্ষা’’ কবিতার অংশ বিশেষ :
‘'আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে/ রেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।’'
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের কবিতা এবং ইরানের কবি ফখররুদ্দিন ইরাকির কবিতা পর্যন্ত প্রসারিত যে চেতনার বীজ, বীজতলা এবং শস্যভূমি। যাপিত জীবনের যে বৃহত্তর পর্যায়ক্রম, তার প্রতিভাস কবিতাজমিনে অঙ্কিত না হলে কবিতা হয়ে পড়ে জীবনবিমুখ। পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে পারেন না অনেক কবিই। জসীমউদ্দীন তাঁর কবিতাকে এই ‘খাঁটি জীবনের’ প্রতিচ্ছায়া করতে গিয়ে সঙ্কটকালীন মানব মনের বলিষ্ঠ বিবেকের মতো সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় বিধৃত সমাজ ও জীবন বুঝতে হলে কবিমনের এই বিশেষ প্রবণতাটি মনে রাখতে হবে। জসীমউদ্দীন ছিলেন প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী এবং এ ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। এ রূপ মানসিকতার কারণেই ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকার রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নিলে অনেকের মতো তিনিও এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি জীবন-সংগ্রামকে কবিতা-কাঁথায় আঁকতে চেয়েছেন বিভিন্নভাবে, বিচিত্র পরিসরে।
জসীমউদ্দীনের কবিতায় লোকবাংলার স্নিগ্ধ নিসর্গ যেমন উঠে এসেছে তেমনই উঠে এসেছে গ্রামবাংলার নানা অসঙ্গতি, শোষণের কথা, অনিয়মের কথা। জেলের বউয়ের মন-খারাপ উঠে আসেঃ
'‘ইচ্ছে করে কলসীটিরে বাঁধি মাথার কেশে,/
ভাসিয়ে দেয় জেলে তাহার রয় যে বে-গান দেশে(জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়)’'।
আসলে তিনি বাংলার মানুষের জীবন-জীবিকার ভাষ্যকার। তাইতো তিনি সহজেই বলতে পারেন,
‘'কাঁদে এই মাটি। আমি শুধু শুনি মাটিতে এ বুক পাতি,/ মাটির বুকের স্পন্দন শুনি, জাগিয়া দীঘল রাতি।’'
গ্রাম বাংলার মানুষের আতিথেয়তা বিশ্ববিখ্যাত। ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতায় জসীমউদ্দীনের স্বর এভাবেই বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে,
‘'তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে, আমাদের
ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়;
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গৃহখানি রহিয়াছে ভরি,
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভাইয়ের
স্নেহের ছায়,
তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে, আমাদের/
ছোট গায়।’'
রূপক, উপমা, প্রতীক, রূপকল্পের বিচিত্র, নৈপুণ্যপূর্ণ ব্যবহার আধুনিক কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আগের যুগেও এর ব্যবহার ছিল। চিরচেনা পরিবেশ নিয়ে জসীমউদ্দীনের কবিতার চিত্রায়ণ খুব স্বাভাবিক বিষয় বলেই মনে হয়। লোকজ উপাদানের এমন কিছু কবিতাংশ তুলে ধরছি:
(১)
"মাঠের যতনা ফুল লয়ে দুলী পরিল সারাটি গায়,
খোঁপায় জড়ালো কলমীর লতা, গাঁদা ফুল হাতে পায়"
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)
(২)
''রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! সারাটা দিন খেলা,
এ যে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।
কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙ্গল দিয়ে খেলি,
নিড়িয়ে দেই ধানের খেতের সবুজ রঙের চেলি।"
(রাখাল ছেল, রাখালী)
উল্লেখিত কবিতাংশ তাঁর কাব্যরীতির প্রতিনিধি ধরে নেওয়াই শ্রেয়। আধুনিক কবিতায় অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। কবি জসীমউদ্দীন কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি ও অন্যান্য অলংকারের ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর অলংকারের বেশিরভাগ উপাদানই লোকজ। উপমা ও অনুপ্রাসের ব্যবহার কবিতার শিল্পগুণকে উন্নীত করেছে।
প্রতিনিধিমূলক কিছু পংক্তি উল্লেখ করছি। প্রথমেই ‘নকশীকাঁথার মাঠ’ থেকে কিছু অলংকারিক(উপমা ও অনুপ্রাস) প্রয়োগ দেখে নিই: ‘কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া’, ‘লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী’, ‘কচি কচি হাত-পা সাজুর সোনার সোনার খেলা,(যমক)/তুলসী তলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঝের বেলা’, ‘তুলসী ফুলের মঞ্জুরী কি দেব দেউলেত ধূপ’, ‘কালো মেঘা নামো নামো, ফুল তোলা মেঘ নামো’, ‘বাজে বাঁশী বাজে, রাতের আঁধারে, সুদূর নদীর চরে,/উদাসী বাতাস ডানা ভেঙে পড়ে বালুর কাফন পরে(সমাসোক্তিসহ)’। অন্যান্য কাব্য থেকে কিছু উদাহরণ টেনে দেওয়া যেতে পারে :
(১)
"চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন পরি।
দুর ছাই,কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি"
(উপমা ও অনুপ্রাস প্রয়োগ, পল্লী জননী, রাখালী)
(২)
'হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নায় জাল পাতি,
টেনে টেনে তবে হয়রান হয়ে, ডুবে যায় সারারাতি"
(সমাসোক্তির প্রয়োগ, নকশী কাঁথার মাঠ)
চরিত্র নির্মাণে (বিশেষত নায়ক-নায়িকা) কবি জসীমউদ্দীন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। উপমার প্রয়োগে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আর অন্ত্যানুপ্রাস তো কবির স্বভাবজাত ঃ
(১)
"সোজন যেনবা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছড়িয়া কূল করে টানাটানি
নামেও সোজন, কামেও তেমনি,শান্ত স্বভাব তার
কূল ভেঙে নদী যতই বহুক, সে তারি গলার হার"
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)
(২) ‘সকিনা’ আখ্যানকাব্যে নায়িকা সকিনাকে নিয়ে নায়ক আদিলের স্বপ্ন; জসীম উদদীনের কবিতায়,
"সকিনারে লয়ে আদিল এবার পাতিল সুখের ঘর,
বাবুই পাখীরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।
স্রোঁতের শেহলা ভাসিতে ভাসিতে একবার পাইল কূল,
আদিল বলিল, ‘‘গাঙের পানিতে কুড়ায়ে পেয়েছি ফুল’’।
এই ফুল আমি মালায় মালায় গাঁথিয়া গলায় পরিয়া নেব,
এই ফুল আমি আতর করিয়া বাতাসে ছড়ায়ে দেব।
এই ফুল আমি লিখন লিখিব, ভালোবাসা দুটি কথা,
এই ফুলে আমি হাসিখুশি করে জড়াব জীবনলতা।"
শিল্পী যতই নিঃসঙ্গ হোন না কেন, তাঁর ব্যক্তি-মানসের সূত্রগুলো সমাজ সংগঠনের ভেতরেই নিহিত থাকে। হিন্দু মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণের কাল যখন ফুরিয়ে এসেছে, বিশ শতকের সেই প্রথম দিকেই মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের উন্মেষ। স্বভাবতই মুসলিম মধ্যবিত্ত তখন অপেক্ষাকৃত আশাবাদী। সুতরাং জসীমউদ্দীনের কবি-মানসে লোকজ জীবন ও ঐতিহ্যের প্রাধান্য কোনো প্রতিক্রিয়া-সজ্ঞাত নয়। বরং বলা চলে বৃহত্তর বাংলার কৃষক সমাজ ও তাদের সংস্কৃতির সাথে জসীমউদ্দীনের পরিচয় ঐতিহাসিক কারণেই প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। গ্রামবাংলা ও তার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য তাঁর কবিতার শুধু উপকরণই নয়; প্রেরণাও বটে। গ্রামীণ গাথা ও পুথি সাহিত্যের আবহাওয়ায় পুষ্ট জসীমউদ্দীনের কাব্য-সাধনায় যে আবহমান বাংলার পরিচয় উদ্ভাসিত তা কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে অসম্পূর্ণ অথবা খণ্ডিত নয়। জসীমউদ্দীনের কবিতায় শুধু গ্রাম আর গ্রামীণ জীবনচিত্র অন্বেষণ এখন নিরর্থক; তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন আজ অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ঐতিহ্যবাহী বাংলা কবিতার মূল ধারাটিকে নগরসভায় নিয়ে আসবার কৃতিত্ব জসীমউদ্দীনের। জসীমউদ্দীন তাঁর কাব্যাদর্শে আজীবন অটল ছিলেন এবং গ্রাম্যতা পরিহার করে গ্রামীণ ভাবাবহে তিনি প্লাবিত করে রেখে গেছেন নগরাক্রান্ত চিত্ত। প্রকৃত অর্থে, গীতলতার অন্তরালে জসীমউদ্দীনের কবিতায় দ্রোহ আছে। আছে প্রতিবাদের অগ্নিশিখা। তিনি নিজস্ব ভাষাভঙ্গিতেই অবলীলায় নির্মাণ করেছেন সে প্রতিবাদের প্রতিভাস। জসীমের বিদ্রোহী-সত্তাটিকে চিনে নিতে হলে পাঠককে একটু সাবধানী হতে হয় বৈকি!
জসীমউদ্দীনের পূর্বজ বাংলার কবিরা গ্রামীণ সমাজ ও জীবনের ছবি এঁকেছেন। এই ঐতিহ্য সূচিত হয়েছে চর্যার কবিদের সময় থেকেই। চর্যাপদকর্তারা পর্বতের কথা বলেছেন, শবর বালিকার কথা বলেছেন- সে বালিকার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ পরিয়ে গলায় গুঞ্জর মালা দিয়েছেন। শবরীর রূপমুগ্ধ শবরের প্রমত্ত আবেগের সৌন্দর্যও প্রকাশ করেছেন। নদী অতিক্রমের চিত্র, নৌকা বাওয়ার চিত্র কিংবা ডোম-ডোমনা আর হরিণ-হরিণীর প্রণয় কথা বর্ণনা করেছেন। গ্রাম-নদী-উপবন-রাখাল আর বাঁশির পুনরাবৃত্তি পাই বৈষ্ণব পদাবলীতে। মধ্যযুগের অপরাপর কাব্যেও গ্রাম জীবনের ছবি পরিবেশিত হয়েছে দারুণ মমতায়। শুধু মধ্যযুগের কথাই বা বলি কেন, আধুনিক যুগেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের প্রকৃতি আর মানুষের কথা লিখেছেন। তাঁদের বর্ণনা ও পরিবেশনা গভীর, আন্তরিক এবং প্রাতিস্বিক। বিশশতকের প্রথমপাদে কবি বন্দে আলীর মিয়ার কবিতায়ও ভিড় করেছে গ্রাম-সমাজ ও জীবনের যাবতীয় আনন্দ ও যন্ত্রণা। জসীমউদ্দীন এদের উত্তরাধিকারী। তবে তাঁর বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন পূর্বসূরিদের তুলনায় অনেক নিবিড়। গ্রামের সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ও গ্রামের প্রকৃতি, স্মৃতিকাতরতা, জীবনের প্রতি মমতা-আসক্তি এবং অনুষঙ্গ তার কবিতায় ফুটে উঠেছে আপন আপন চারিত্র্যে।
বাংলাসাহিত্যের তিন বরেণ্যকবি----- কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯) ও জসীমউদদীন (১৯০৩)—জন্ম প্রায় একই সময়ে। কিন্তু তাঁদের স্টাইলে ভিন্নতা ছিল। ফলে তিনজনই টিকে আছেন স্বমহিমায়। নজরুলর বিদ্রোহী সুর আর জীবনানন্দের প্রকৃতির অবগাহনের পাশাপাশি জসীমউদদীন গ্রামীণ সংস্কৃতির ছবি এঁকেছেন কবিতায়। গ্ৰাম বাংলার মাটি ও মানুষের কথা তাঁর কবিতায়। তিনি গ্রামীণ বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়েই নির্মাণ করেছেন তাঁর অসামান্য কালোত্তীর্ণ সব কবিতা।।
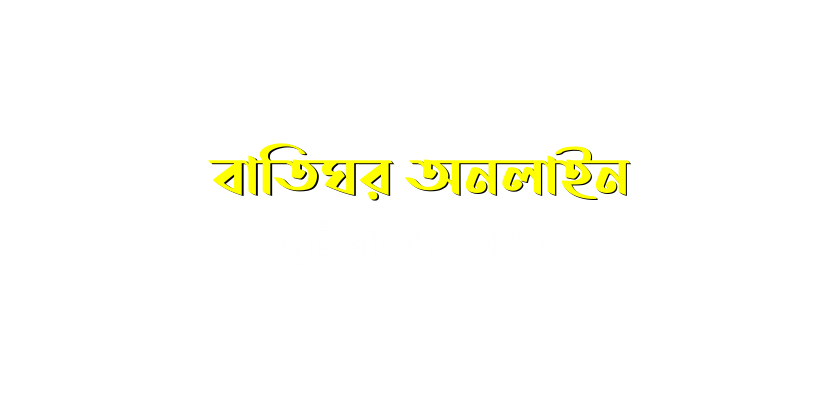





মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন